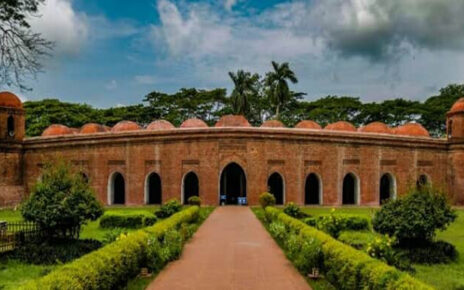নদী, খাল, বিল কিংবা জলাশয়ের বুকে যখন হালকা বেগুনি রঙের কচুরি ফুল ফোটে, তখন দৃশ্যপট নিঃসন্দেহে মোহিত করে চোখ। অথচ এই স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এক দীর্ঘ ও রুদ্ধশ্বাস ইতিহাস। যা একসময় বাংলার কৃষি, নদীপথ ও জনস্বাস্থ্যকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছিল। এই কচুরিপানা, যা ‘বিউটিফুল ব্লু ডেভিল’ এবং ‘বেঙ্গল টেরর’ নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল, তা এখন পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও কুটিরশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তবে এই রূপান্তরের পেছনে রয়েছে প্রায় দেড়শ বছরের লড়াই ও অভিযোজনের গল্প। বর্তমান বাংলাদেশে যেসব সবুজ পাতার ভেলা আর হালকা বেগুনি ফুলওয়ালা কচুরিপানা জলাশয় জুড়ে দেখা যায়, এগুলোর কোনো প্রাকৃতিক অস্তিত্ব ছিল না এই অঞ্চলে। মূলত এই উদ্ভিদ এসেছে হাজার হাজার মাইল দূরের দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন জলাভূমি থেকে। এই আগমনকে ঘিরে নানা মতভেদ রয়েছে। বাংলাপিডিয়া অনুযায়ী, ১৮৮৪ সালে ব্রাজিল থেকে জর্জ মরগান নামের এক স্কটিশ ব্যবসায়ী এর ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কচুরিপানা বাংলায় নিয়ে আসেন। আরেকটি সূত্র মতে, এটি এসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে এক নারায়ণগঞ্জের পাট ব্যবসায়ীর হাত ধরে। আবার কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের বার্ষিক প্রতিবেদনে এর আগমনকাল ধরা হয়েছে ১৮৯০ দশকের কাছাকাছি সময়ে। কচুরিপানার সমস্যার মূল কারণ ছিল এর বিস্তারের গতি। মাত্র ৫০ দিনে একটি কচুরিপানা উদ্ভিদ তিন হাজারের বেশি সংখ্যায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই ভয়ানক বৃদ্ধির ক্ষমতা ১৯২০ সালের মধ্যেই বাংলার জলপথগুলিকে প্রায় অচল করে তোলে। নদী-নালা-পুকুর সবই কচুরিপানায় ছেয়ে যায়। কৃষিকাজে জল ব্যবহার, মাছ ধরা, নদীপথে পণ্য পরিবহন সবকিছুই বাধাগ্রস্ত হতে শুরু করে। কচুরিপানার পচনশীল অংশ থেকে উৎপন্ন বিষাক্ত গ্যাস পানিতে মিশে জলজ প্রাণীদের হত্যা করে। মানুষও এই পানি ব্যবহার করে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে শুরু করে। এনোফেলিস মশার আবাসস্থল হওয়ায় ম্যালেরিয়া রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, এর প্রভাবে ৩০ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল বলেও অনেক গবেষক মত দেন, যা এক মহামারির রূপ নিয়েছিল। এভাবেই একসময় সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে ওঠা এই কচুরিপানা বাংলা অঞ্চলের এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল, যার কারণে একে ‘বিউটিফুল ব্লু ডেভিল’ নামে অভিহিত করা হয়। এই সংকট মোকাবেলায় ব্রিটিশ প্রশাসন নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯১৬ সালে ‘ওয়াটার হায়াসিন্থ কমিটি’র উদ্যোগে গবেষণা শুরু হয়। গবেষণায় দেখা যায়, কচুরিপানায় প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন, পটাশ ও ফসফরিক এসিড রয়েছে। এই আবিষ্কারের ফলে কচুরিপানাকে জৈব সার, পশুখাদ্য ও রাসায়নিক উপাদানের কাঁচামাল হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যবহারের চিন্তা শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন বিশ্ববাজারে পটাশের সংকট দেখা দেয়, তখন কচুরিপানাই সেই ঘাটতি কিছুটা পুষিয়ে দেয়। কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক ব্যবহার বাড়িয়েই এই উদ্ভিদের বিস্তার ঠেকানো যায়নি। ১৯২১ সালে গঠিত হয় ‘কচুরিপানা নির্মূল কমিটি’। কমিটি গবেষণা চালিয়ে গেলেও ফলপ্রসূ সমাধান আসে না। ফলে ১৯৩৬ সালে ‘কচুরিপানা বিধি’ চালু করা হয়। এই বিধির আওতায় প্রত্যেক নাগরিককে নিজ এলাকার কচুরিপানা পরিষ্কার করা বাধ্যতামূলক করা হয়। এমনকি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোও কচুরিপানা নির্মূলের প্রতিশ্রুতি দেয়। নির্বাচনের পর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৩৯ সালে ‘কচুরিপানা সপ্তাহ’ পালনের মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করেন। এসব উদ্যোগের ফলে কচুরিপানার দাপট কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে ১৯৪৭ সালের পর। যে কচুরিপানার কারণে একসময় বাংলার আর্থসামাজিক ভিত্তি টলে গিয়েছিল, সে কচুরিপানা আজ আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় পরিবেশ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে বায়োমাস থেকে বায়োফার্টিলাইজার তৈরিতে কচুরিপানা ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে উচ্চমাত্রার নাইট্রোজেন থাকার কারণে এটি জৈব সারের কার্যকর উৎস হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি বায়োগ্যাস উৎপাদনেও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। হাওর অঞ্চলে এই কচুরিপানা ঢেউ ঠেকানোর জন্য বিশেষভাবে চাষ করা হয়, যা ফসলি জমি রক্ষায় ভূমিকা রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে, কচুরিপানার কাণ্ড দূষিত পানির বিভিন্ন ভারী ধাতু যেমন—ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, সীসা, কোবাল্ট ইত্যাদি শোষণ করতে সক্ষম, যা পানিকে কিছুটা বিশুদ্ধ করে তোলে। তাছাড়া গ্রামীণ অঞ্চলে কুটিরশিল্পেও কচুরিপানার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। এর ফাইবার ও ডাঁটা দিয়ে তৈরি হ্যান্ডিক্র্যাফট, ঝুড়ি, চট ইত্যাদি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কচুরিপানার পাতা, শিকড় এবং কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ প্রসাধনী, পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিং, এবং ঘর সাজানোর সামগ্রীর কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, যে উদ্ভিদ একসময় বাংলার কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবহনব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছিল, আজ তা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হয়ে উঠেছে সম্ভাবনার প্রতীক। ‘বিউটিফুল ব্লু ডেভিল’ আজ শুধু ‘বিউটিফুল’ হয়েই থেকে যায়নি, বরং তা বাংলার নতুন অর্থনৈতিক দিগন্ত উন্মোচনে সহায়ক হয়ে উঠেছে। তবে এর ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের বাইরে কোনো কিছু শখের বশে আনা কতটা ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। সেই শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক।
– ইমরুল কায়েস