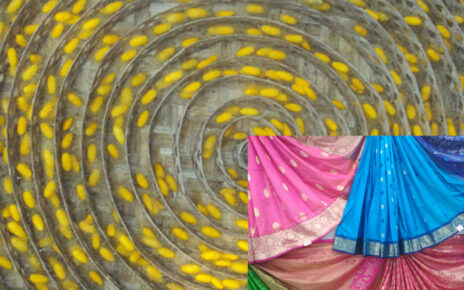সাহিত্য কাকে বলে? সাহিত্য বলতে আমরা সমাজে মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রীতি-বিশ্বাস, ন্যায়-নিষ্ঠা ইত্যাদির বাস্তব রূপায়ণ বুঝি, যা দেশ-জাতির হৃদয়ের কথা বলে। সে ধরনের সাহিত্য যে দেশে যত শক্তিশালী, সে জাতির জীবনবোধ তত গভীর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, সাহিত্যে উচ্চকিত হয়েছে জাতির মুক্তি ও প্রগতির বার্তা। সাহিত্যে জাতীয় জীবনের অতীত ঐতিহ্য, বর্তমান সংকট এবং ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার রূপায়ণ থাকে বিধায় সাহিত্যই জাতীয় জীবনের দর্পণ, যার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় জাতির সর্বসত্তাকে। সাহিত্যের মধ্যেই নিহিত সমাজের বাস্তব ববিদ প্রতিরূপ। আর সাহিত্য পাঠের মাধ্যমেই সব বিষয়ে ধারণা পাওয়া সম্ভব। কেননা সবকিছুকে ধারণ করতে পারে একমাত্র সাহিত্য।
সাহিত্য কী বা সাহিত্যের সংজ্ঞা নিয়ে সাহিত্যরসিক কবি সাহিত্যিকরা তাঁদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। সেইসব মতের ভিন্নতা থাকলেও তা একই সূত্রে গাঁথা। কবি Mathew Arnold সাহিত্য বা কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অতি সংক্ষেপে একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করেছেন এবং সেটি হচ্ছে, poetry is the Criticism of life অর্থাৎ- কবিতা বা সাহিত্য হচ্ছে জীবনের বিশ্লেষণ বা সমালোচনা। সাহিত্যের জন্ম প্রকৃতভাবে কবে, কোথায় হয়েছে সেটি সঠিক ভাবে বলা যায় না। প্রকৃতি, পরিবেশ, প্রাণী, নদী, নারী, ফুল, পাখি, বাস্তব- পরাবাস্তব অভিজ্ঞতা ও কল্পনাই হচ্ছে সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার প্রকাশই হচ্ছে সাহিত্যের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মানুষ, জাতি তথা সভ্যতার বিকাশে সর্বাপেক্ষা অবদান সাহিত্যের। সাহিত্যের মধ্যেই প্রতিফলিত হয় জাতির সংস্কৃতি, সমাজ সভ্যতা। যে জাতির সাহিত্য যত বেশি সমৃদ্ধ, সে জাতি তত উন্নত। কারণ সাহিত্য জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। সাহিত্য একটি জাতির জীবনের কথা বলে। সাহিত্য জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। একটি জাতি কী, তা তার সাহিত্য-সংস্কৃতিই বলে দেয়। সাহিত্যই হচ্ছে একটি জাতির জীবনাচরণের দলিল। সাহিত্যই জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। সাহিত্য যেহেতু জীবনের কথা বলে, সুতরাং আগে জীবন, তারপর সাহিত্য। সাহিত্য কেবল একটি জাতির বর্তমান চিন্তা-ভাবনাকেই চিত্রায়িত করে না; বরং সাহিত্য একটি জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকেও উচ্চারণ করে। প্রত্যেক জাতির চাওয়া-পাওয়া, তাদের প্রত্যাশা, গড়ে ওঠা, বেড়ে ওঠার রূপায়ণের দায়িত্ব পড়ে সে জাতির কবি-সাহিত্যিকদের ওপর। তাঁরা নানাভাবে শিল্পসম্মতভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
মিশরীয় সভ্যতার আদিমকালে কোনো বর্ণ বা অক্ষর ছিলো না। ছবির সাহায্যে তারা পরস্পর মত বিনিময় করতো বা পার্থিব ঘটনার পরিচয় তুলে ধরতো। এরপর আমরা আসিরীয় সভ্যতা মেসোপোটমিয়া সভ্যতা, ব্যবলনীয় সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, ভারত সভ্যতা ইত্যাদির বিকাশ ঘটতে দেখি। মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা বা কথামালারও উন্নয়ন ঘটে। আসিরীয় যুগে গিলগ্যামেশ নামক এক সম্রাট ছিলো, তিনি বিলগামেস নামেও পরিচিত। তারই নামে রচিত হয় বিশ্বসাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য গিলাগামেশ। সে যুগে কাগজ ছিলো না। মানুষ প্রাচীন লিপি পাথর, পাহাড় বা বৃক্ষকাণ্ডে লিখে রাখতো। এর বহুকাল পরে মানুষ গাছের পাতা, পশুর চামড়া বা ঐ জাতীয় বস্তুতে লেখার প্রচলন শুরু করে।
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নাম উঠলে প্রথমে প্রমথ চৌধুরী নাম উঠে আসে। চিঠিপত্র লেখা এবং দলিল-দস্তাবেজ লেখার প্রয়োজনে বাংলা গদ্যের সূত্রপাত। বাংলা গদ্য শুরুতে ছিল সংস্কৃতি গদ্যের চালে রচিত যার প্রমাণ বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ। বলা যায়, বিশিষ্ট গদ্যকার প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যকে একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন। লেখার ভাষাকে জনবান্ধব ও সহজবোধ করে তোলা অর্থাৎ সাহিত্যে চলিত ভাষা প্রচলনের কৃতিত্ব অনেকাংশেই তার। বাংলা সাহিত্যে আছে লোকসাহিত্য, আছে শিশুসাহিত্যের মতো সমৃদ্ধ ধারা, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ বাংলাসাহিত্যে যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা। এই ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অনেক সাহিত্য। সেগুলোতে আমাদের হাজার বছরের পুরনো বাংলাসাহিত্যকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করে, সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা, চেতনা, যোগ হচ্ছে। ফলে নতুনকে গ্রহণ করে, নতুন-পুরাতনের সংমিশ্রণে আমাদের সাহিত্যাকাশ হয়ে উঠেছে আরও বৈচিত্র্যময়।
– মোহাম্মদ জাহিদ